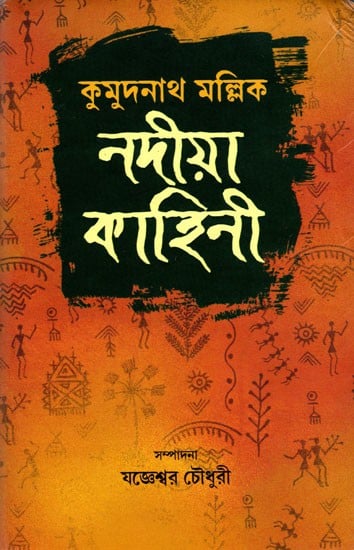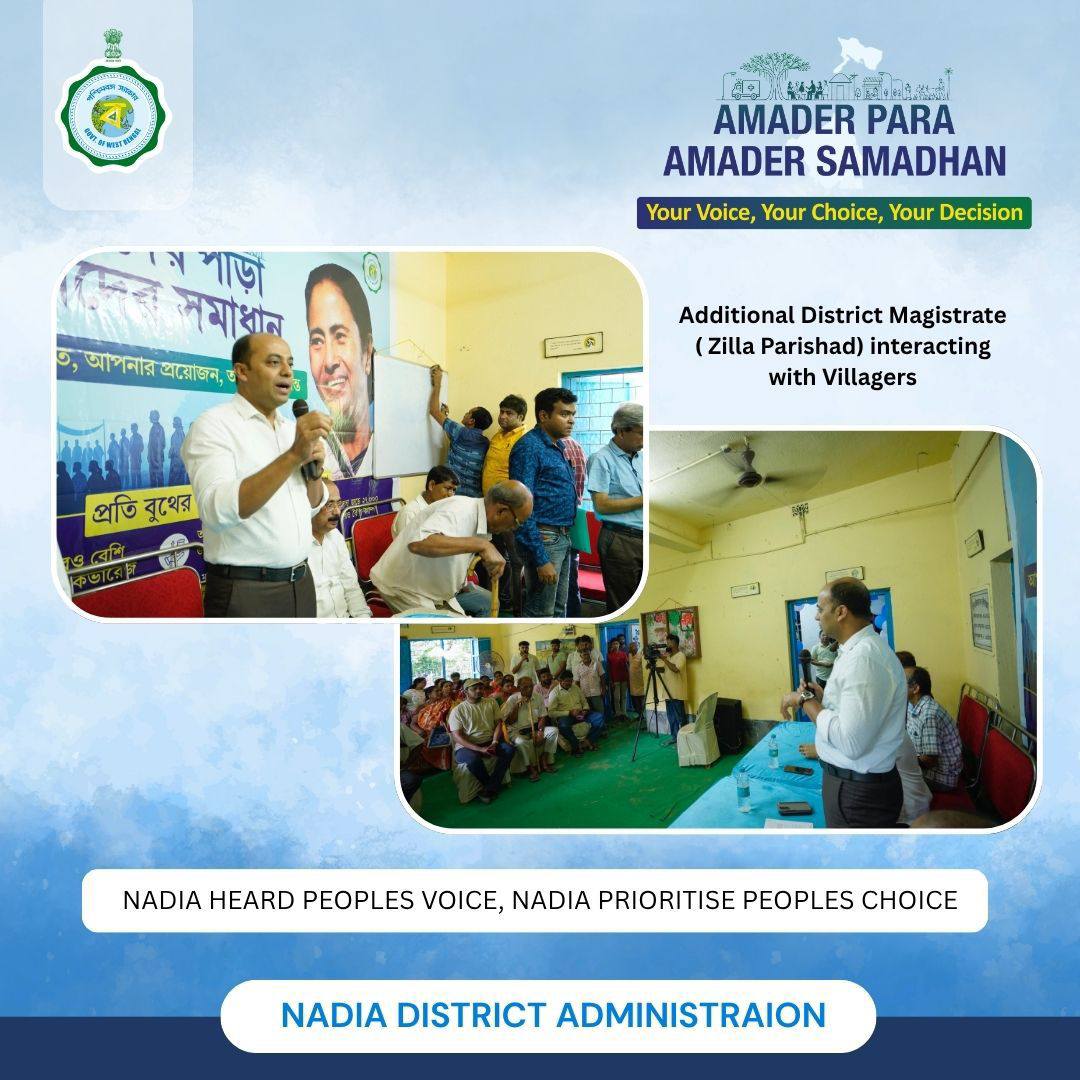বাংলা সাহিত্যে কুমুদনাথ মল্লিক রচিত নদীয়া-কাহিনী একটি বিরল ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে (১৯১২ খ্রিস্টাব্দ) রানাঘাট থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি কেবল নদীয়া জেলার ইতিহাস নয়, বাংলা ভাষায় রচিত আঞ্চলিক ইতিহাসের ক্ষেত্রেও একটি পথপ্রদর্শক গ্রন্থ। পূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ সংকলিত করে তৈরি করা এই গ্রন্থে লেখক স্থানিক ইতিহাস, সমাজচিত্র, ধর্মীয় ধারা এবং সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে একত্রে বিশ্লেষণ করেছেন।
এই গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তার রচনাশৈলী—এটি নিছক তথ্যভিত্তিক ইতিহাস নয়, বরং ইতিহাস, অনুভব এবং ভাষার মেলবন্ধনে এক প্রান্তিক অঞ্চলের জাগ্রত আত্মপরিচয়। নদীয়া জেলার ভৌগোলিক পরিচয়, রাজনৈতিক উত্থানপতন, সাহিত্য ও ধর্মীয় পরম্পরা, এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার অন্তরঙ্গ বিবরণ এখানে অনুপুঙ্খভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কুমুদনাথ মল্লিক একাধারে ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল পর্যবেক্ষক ছিলেন, যার ছাপ প্রতিটি অধ্যায়ে অনুভূত হয়।
গ্রন্থে মধ্যযুগীয় নদীয়ার বর্ণনা অত্যন্ত মনোগ্রাহী। লেখক বিশেষভাবে হুসেন শাহের শাসনকাল (১৪৯৪–১৫১৯ খ্রিঃ) নিয়ে আলোচনা করেছেন, যেটিকে তিনি বঙ্গসাহিত্যের ‘সোনালি যুগ’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই সময়ে কবি পরমেশ্বর কর্তৃক মহাভারতের অনুবাদ পারগলী ভারত, ছুটী খাঁ ও গুণরাজ খাঁ প্রমুখের সাহিত্যকর্ম, এবং বাংলার ভাষাভিত্তিক সাহিত্যচর্চার প্রসারে নদীয়ার ভূমিকাকে তিনি অনন্য বলে বিবেচনা করেছেন (মল্লিক, পৃ. ৩৮–৪১; খান, ২০১১)।
নদীয়ার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আলোচনাতেও লেখক সমান সাবলীল। কাঞ্চনপল্লীতে জন্মগ্রহণকারী কবিকর্ণপুর বা শ্রুতিধর নিমচাঁদ শিরোমণির মতো ব্যক্তিত্বের কথার মাধ্যমে নদীয়ার আধ্যাত্মিক বাতাবরণ ও সংস্কৃতিচর্চার গভীরতা ধরা পড়েছে (মল্লিক, পৃ. ৪০১–৪০৩; গাঙ্গুলী, ১৯৯৫)। এসব তথ্য শুধু ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে না, পাঠককে পরিচয় করায় এক বিস্মৃত সাংস্কৃতিক মানচিত্রের সঙ্গে।
এছাড়া এই গ্রন্থে স্থানীয় জনজীবনের বিবরণ, রোগব্যাধি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব নিয়ে এক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণও পাওয়া যায়। শান্তিপুরের গাধানগর এলাকার জনসংখ্যা একসময় ৫০,০০০ থাকলেও ম্যালেরিয়ার প্রভাবে তা হ্রাস পেয়ে ৩,৫০০-এ নেমে আসে—এটি কেবল পরিসংখ্যান নয়, বরং একটি জনপদের পতন ও পরিবর্তনের ইতিহাস (মল্লিক, পৃ. ৩৭০; গোস্বামী, ২০০৩)। এমনকি স্থানীয় বসতি, চাষবাস, ধর্মীয় অনুশীলন ও শিক্ষা ব্যবস্থার বিবরণেও লেখক সমাজের গভীরতর স্তরে প্রবেশ করেছেন।
এই প্রবন্ধসংকলনের ভাষা নিজেই এক গবেষণার বিষয়। লেখকের ভাষা কখনও ব্যঙ্গাত্মক, কখনও রসঘন, কখনও আন্তরিক, কখনও গভীর ব্যথায় পূর্ণ। কুমুদনাথ মল্লিকের রচনার গঠন এবং শব্দচয়ন বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ধারা নির্মাণ করেছে (সান্যাল, ১৯৮০)। সাহিত্যিক উপমা, রম্যরস এবং আত্মদৃষ্টিকোণ থেকে লেখা তাঁর উপস্থাপনা পাঠককে শুধু তথ্যের স্তরে রাখে না, বরং আবেগ ও চিন্তনের জগতে প্রবেশ করায়।
নদীয়া-কাহিনী তাই কেবল একটি স্থানীয় ইতিহাস নয়, এটি ইতিহাস, সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির এমন এক সংমিশ্রণ যেখানে নদীয়ার অতীত জীবন্ত হয়ে ওঠে। আজও এই গ্রন্থ গবেষকদের জন্য একটি প্রাথমিক ও মূল্যবান উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই রচনাটি বাংলা ভাষার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত হয়ে আছে, যা Internet Archive ও Wikisource-এর মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সহজে উপলব্ধ।
একবিংশ শতাব্দীর পাঠকের কাছে নদীয়া-কাহিনী এক ‘লোকস্মৃতির পুনরুদ্ধার’। কুমুদনাথ মল্লিকের গভীর পর্যবেক্ষণ, ঐতিহাসিক তথ্যের নিখুঁত বিন্যাস এবং ভাষার সাহিত্যিক ভঙ্গিমা এই গ্রন্থকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। বাংলা সাহিত্যের পরিমণ্ডলে এমন প্রয়াস শুধু অতীতের অনুরণন নয়, ভবিষ্যতের দিকনির্দেশও বটে।
তথ্যসূত্র
-
মল্লিক, কুমুদনাথ। নদীয়া-কাহিনী, অগ্রদূত প্রেস, রানাঘাট, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।
Wikisource সংস্করণ
-
খান, মোঃ হুমায়ুন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১১।
-
গাঙ্গুলী, অমলেন্দু। নবদ্বীপ: তীর্থ ও তর্কভূমি, বিশ্বভারতী, ১৯৯৫।
-
গোস্বামী, রঞ্জন। বাংলার সামাজিক ইতিহাস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩।
-
সান্যাল, হেমচন্দ্র। বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য, নব্যভারতী, ১৯৮০।